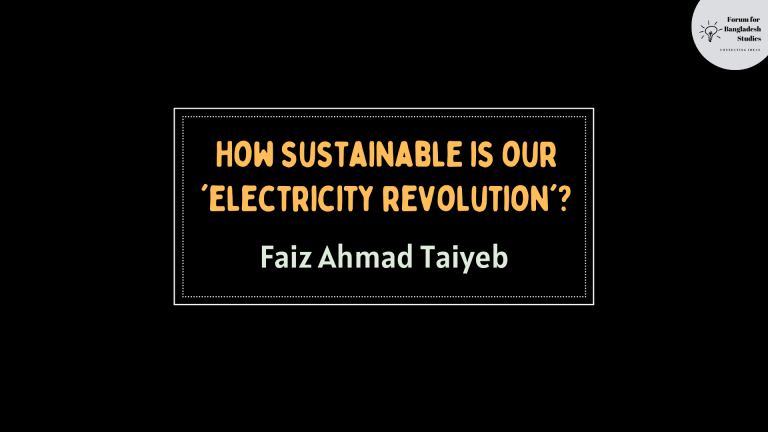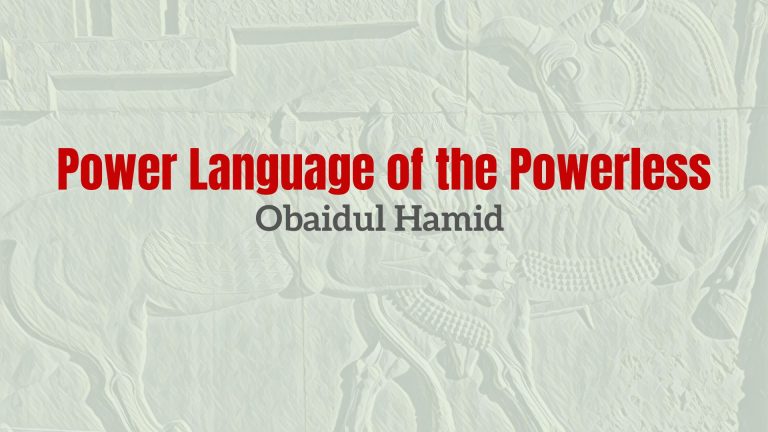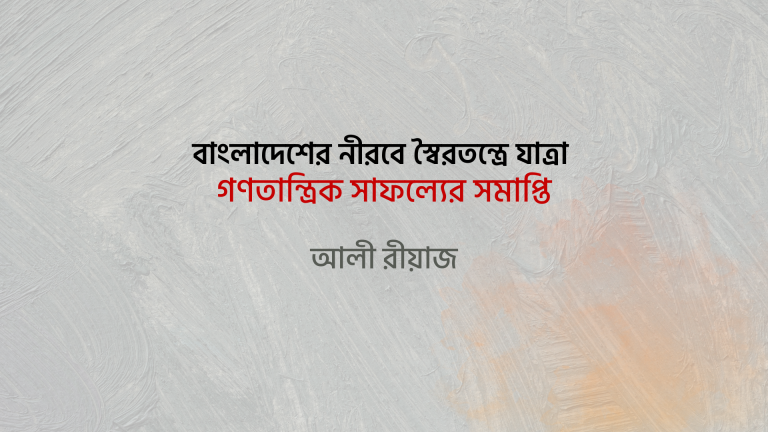‘দিল্লি আছে, আমরা আছি’
নয়াদিল্লিতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনায় বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা এক অর্থে এটাই দেখায় যে বাংলাদেশের নাগরিকদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ বাংলাদেশের নাগরিকদের হাতে নেই, যা বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক নয়। কিন্তু এ নিয়ে ক্ষমতাসীনেরা উচ্চবাচ্য করেনি।
এর ফলে এই প্রশ্ন তোলার অবকাশ তৈরি হয় যে বাংলাদেশের সরকার কতটা স্বাধীন? (মাহ্ফুজ আনাম, ডেইলি স্টার বাংলা, ৬ অক্টোবর ২০২৩)। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের আলোচনার পর দৃশ্যত বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের মধ্যে একধরনের আশাবাদ তৈরি হয়েছে।
তাঁদের আশাবাদের ভিত্তি হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রার মন্তব্য। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি আমরা। বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সে দেশের মানুষ তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। একটি বন্ধু এবং সঙ্গী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান জানাই আমরা।’ (বিবিসি বাংলা, ১০ নভেম্বর ২০২৩)
এই মন্তব্য এবং দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর প্রকাশিত বিবৃতিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে আগে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের যে দাবি করেছিলেন, ‘তলেতলে আপস হয়ে গেছে। দিল্লি আছে, আমেরিকারও দিল্লিকে দরকার। দিল্লি আছে, আমরা আছি।’ (ডেইলি স্টার বাংলা, ৩ অক্টোবর ২০২৩), তা সঠিক ছিল না। সম্ভবত ক্ষমতাসীনদের আশঙ্কা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ভারত তার অবস্থান বদলে ফেলবে।
তেমন কিছু না ঘটাকেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এমনভাবে উপস্থাপন করছেন, যাতে মনে হয়, আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে ভারতের এই অবস্থান ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় যেমনভাবে ক্ষমতাসীনদের সুরক্ষা করেছে, তেমনটিই হবে। আসন্ন নির্বাচন—তা যদি সাজানো এবং অগ্রহণযোগ্যও হয়, তারপরও ভারত তাঁদের সুরক্ষা করবে, সেটাই তাঁদের আশা এবং কৌশল। ওবায়দুল কাদের এ–ও বলেছিলেন যে ‘চিন্তার কিছু নেই’। তাঁর এই মন্তব্যের পরে সংগত কারণেই এটাই মনে হয়েছিলে যে ওবায়দুল কাদের বলছেন, বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকার জন্য দিল্লির সমর্থনই যথেষ্ট।
এ ধরনের কথাবার্তার কারণ হচ্ছে ভারতের সঙ্গে এক অসম সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, যে পর্বের সূচনা হয়েছে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই। এ ধরনের মন্তব্যের আগে গত বছরের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছিলেন, ‘আমি ভারতে গিয়ে বলেছি যে শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করার, সে জন্য ভারতবর্ষ সরকারকে আমি সেই অনুরোধ করেছি।’ (বিবিসি বাংলা, ১৯ আগস্ট ২০২২)।
এ ধরনের কথাবার্তা নেহাতই কথার কথা নয়। ভারতের ওপরে নির্ভরতার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে সরকারের বিরোধীদের যেভাবে দমন করা হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে কার্যত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং নাগরিকদের মৌলিক ভোটাধিকার যেভাবে পদদলিত হয়েছে, তাতে করে দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি অনুপস্থিত।
২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে যে রাজনৈতিক দলগুলোকেই কেবল নির্বাচনের বাইরে রাখার জন্য ক্ষমতাসীনেরা সফল হয়েছে তা নয়, যেকোনো নির্বাচনের সবচেয়ে বড় অংশীদার যে ভোটার, তাঁদেরও বাইরে রাখা হয়েছে। এর ফলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার নামে ২০২৪ সালে নির্বাচন হলেই তাতে ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন, সেটার সম্ভাবনা নেই। তার জন্য দরকার নির্বাচনকালীন এমন একধরনের ব্যবস্থা, যা ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র আধিপত্য, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে পারে।
বিরোধী দলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি জানিয়ে আসছে। দেশের নাগরিকদের একটি বড় অংশই যে তা মনে করেন, তার প্রমাণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) করা জরিপ, যাতে ৪৪ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দরকার। ২০১১ সালে একপক্ষীয়ভাবে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত আরও ২৫ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে সব দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের অধীনে নির্বাচন করা দরকার। অর্থাৎ, সব মিলে ৬৯ শতাংশ মানুষ মনে করেন, বিরাজমান ব্যবস্থায় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না।
ক্ষমতাসীন দলের নেতা–কর্মীরা এই দাবি উপেক্ষা করে যে কথা বলছেন, তা হচ্ছে তাঁদের অধীনেই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হতে হবে। তা যে অসম্ভব, তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। নির্বাচন কমিশন এসব ব্যর্থতার দায় না নিয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছে ‘যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করতে হবে’ (কালবেলা, ১০ নভেম্বর ২০২৩)
অতীতে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষমতাসীনেরা ‘নির্বাচনের মূল্য’ হিসেবে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারকেই জলাঞ্জলি দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন যদি গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ করে ভেঙে দেওয়া, বিএনপি নেতা-কর্মীদের বেশুমার আটক-মামলা-নিপীড়ন এবং ক্রমাগত সহিংসতাকেই ‘যেকোনো মূল্য’ বলে বিবেচনা করে এবং তাকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মনে করে, কেবল তবেই বলা সম্ভব যে যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করতে হবে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রাসঙ্গিকতা
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির এই আলোচনায় ভারতের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? কেউ কেউ সেই প্রশ্ন করতে পারেন। ২০০৯ সাল থেকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এ ধরনের নির্বাচন এবং শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র। যদিও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেছেন, ‘বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সে দেশের মানুষ তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।’
কিন্তু গত ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিশ্লেষণ এবং ইউটিউবে প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের আলোচনায় দেখা যায় যে তারা চাইছে, ভারত যেকোনো অবস্থাতেই যেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে (আলী রীয়াজ, ‘বাংলাদেশ ইলেকশন ২০২৪: হোয়াট রোল উইল ইন্ডিয়া প্লে?’, আটলান্টিক কাউন্সিল, ১৫ জুন ২০২৩)
এ ধরনের বক্তব্যের সময় তাঁরা ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সামনে আনলেও এ কথা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই, গত ৯ বছরে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে চেয়ে পায়নি, এমন কিছুই নেই। এই অসম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা জনগণের ম্যান্ডেটের ওপরে নির্ভর করেনি। অবাধ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি উপস্থিত থাকলে অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তার যেসব সুবিধাদি ভারত পেয়েছে, তার একটি বড় অংশের ব্যাপারে প্রশ্ন থাকত।
ভারতের এই প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ২০০১ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অনাগ্রহ এবং ভারতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাজনীতিকে দেখার নীতির কারণে। যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারতকেই তার প্রতিনিধি ভেবেছে। কিন্তু তা যে কার্যকর হয়নি, তার সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ‘চীনপন্থী’ বলে পরিচিত মোহাম্মদ মুইজ্জির বিজয়। গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্র এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারতের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর, এমনকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও।
কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত এখনো বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চেয়ে, অবাধ নির্বাচনের চেয়ে এমন সরকার আশা করে, যার ম্যান্ডেট প্রশ্নবিদ্ধ থাকার কারণে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক নির্ভরতা ভারতের ওপরেই থাকবে। এই নির্ভরতা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি বড় অংশই মনে করেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের সমর্থন হ্রাস পেলে ক্ষমতাসীনদের আচরণে পরিবর্তন ঘটবে। এই ধারণার বিষয়ে ক্ষমতাসীনেরা অবহিত। যে কারণে ওবায়দুল কাদের নির্দ্বিধায় বলেন, ‘দিল্লি আছে, আমরাও আছি’; বলেন, ‘চিন্তার কিছু নেই’।
একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে যারাই ক্ষমতায় আসবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে নির্বাচনে ক্ষমতার হাতবদলের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে একধরনের ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ সম্ভব হবে। এই ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম ভিত্তি হবে বাংলাদেশকে ‘ভারতবেষ্টিত’ একটি দেশ হিসেবে বিবেচনা না করে পূর্বমুখী করে তোলা।
বঙ্গোপসাগরের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বকে ব্যবহার করে বিকাশমান ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলোর অর্থনীতি, ওই অঞ্চলের ভূকৌশল এবং নিরাপত্তাকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। লক্ষণীয় যে ভারত তার পররাষ্ট্র এবং নিরাপত্তানীতিসমূহ সেভাবেই সাজিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নির্ভরতা ভারতের ওপরে থাকুক।
যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এর বিপরীতে; গত দেড়–দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেওয়া বার্তা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সরকার দেশের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করুক। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকেরা কর্তৃত্ববাদী আদর্শের বিরুদ্ধেই অবস্থান নেবেন, যার প্রতিফলন কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই পড়বে, তা নয়, পররাষ্ট্রনীতিতেও পড়বে।
নয়াদিল্লিতে যে আলোচনা, তা প্রতিপক্ষের মধ্যকার আলোচনা নয়; ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম দেশ। কিন্তু আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিবেচনায় দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে এই আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেখানে ভারত তার অবস্থান বলেছে; যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে একমত হয়েছে, এমন লক্ষণ নেই। তার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের মানুষের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের পথগুলো এতটাই সরু এবং অমসৃণ করে ফেলা হয়েছে এবং তার পেছনে ভারতের সমর্থন ও স্বার্থই প্রাধান্য পাচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশের নির্বাচন কেমন হবে, সেই বিষয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ অনুপস্থিত, বিদেশিরাই পথরেখা ঠিক করছে।
আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মেরুকরণ
বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন সামনে রেখে গত দেড় বছরে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর একধরনের মেরুকরণ ঘটেছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো বারবার বলে আসছে যে তারা চায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। অন্যদিকে রাশিয়া ও চীন এ ধরনের বক্তব্যকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বলেই বর্ণনা করেছে এবং তারা যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে, তা নিয়ে রাখঢাক করছে না। নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যারা বাধা দেবে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসা দেবে না বলে নীতি ঘোষণা করেছে এবং তার বাস্তবায়নও শুরু করছে।
গত দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যত প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফর করেছেন, কিংবা বাংলাদেশ সরকারের যত প্রতিনিধি সরকারিভাবে ওয়াশিংটন সফর করেছেন, তাঁদের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়েছে আসন্ন নির্বাচন। যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের সবাই এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বারবার বলছেন যে আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ যে তাতে আস্থা রাখতে পারছে না, তা তাদের কথাতেই সুস্পষ্ট।
এ ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা প্রায়ই এ অভিযোগ করছেন যে বিদেশি শক্তিগুলো, যা আসলে প্রকারান্তরে পশ্চিমা দেশগুলোকে বোঝায়, তারা হস্তক্ষেপ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য এবং পদক্ষেপকে ‘প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ’ বলার ক্ষেত্রে ভারতের গণমাধ্যমের বিশ্লেষকেরা এগিয়ে আছেন।
এটা ধরে নেওয়া যায় যে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গুমের শিকার এক ব্যক্তির বাড়িতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে নতুন করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশিদের আগ্রহ এবং কথিত হস্তক্ষেপের আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতারা একে ভিয়েনা কনভেনশনের বরখেলাপ বলেও উল্লেখ করেছেন। এ সময়ই যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তাব্যবস্থা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রাশিয়ার ঢাকা দূতাবাস টুইটারে এবং পরে মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের সমালোচনা করা হয়। মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি ঘোষণার পর চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পরোক্ষ সমালোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের ‘পাশে থাকার’ ঘোষণা দেওয়া হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৭ জুলাই ২০২৩ সংসদের একটি উপনির্বাচনের পরে ১৩টি দেশের কূটনীতিকেরা বিবৃতি দিলে তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে নিয়ে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।
এসব ঘটনার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্যরা দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং হোয়াইট হাউসে চিঠি দিয়েছেন। একই ধরনের ঘটনা ঘটছে ইউরোপেও; ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং কয়েকজন সদস্য আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন।
আর এসব নিয়ে বাংলাদেশের সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা বলেই যাচ্ছেন। একদিকে তাঁরা বলছেন বিদেশিদের কিছুই করার নেই, অন্যদিকে বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘সেলফি’তে ‘কেল্লা ফতে’ হয়ে গেছে। কখনো বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। কখনো বলা হচ্ছে, এই নীতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশী ‘হস্তক্ষেপ’ এর ইতিহাস
বাংলাদেশের রাজনীতি এবং নির্বাচন বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের আগ্রহ এবং সংশ্লিষ্টতার একটা পটভূমি আছে। বিষয়টি এমন নয় যে এই প্রথমবারের মতো বিদেশিরা এসব নিয়ে কথা বলছেন। ১৯৮২ সালে দেশে সেনাশাসন জারির পর রাজনৈতিক দলগুলো যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, তাতে দমন–পীড়ন চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নিয়মিতভাবেই বিদেশি কূটনীতিকদের অবহিত করত।
১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের সরকারবিরোধী দলগুলোর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্য স্টিফেন সোলার্জ ফরেন অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাক্টে এই সংশোধনী যুক্ত করার প্রস্তাব দেন যে বাংলাদেশে মার্কিন সহযোগিতার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্ত যুক্ত করে দেওয়া হোক। গণতন্ত্রের লক্ষণ হিসেবে যে পাঁচটি কথা বলা হয়েছিল, তার প্রথমটি ছিল বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন, ‘যাতে জনগণের মতের প্রতিফলন থাকবে’। এই লক্ষ্যে ১৪ জুলাই ১৯৮৮ কংগ্রেসের শুনানিও হয়েছিল। এ ধরনের উদ্যোগ ইউরোপেও ছিল।
১৯৯৪ সালে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংবিধানে স্থায়ীভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের সূচনা করলে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সূচনা হয়। যার সমাধানের উদ্যোগ নিতে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা আনিয়াওকু বাংলাদেশে আসেন এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত করেন।
পরে কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান মার্টিন স্টিফেনকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্বও দেওয়া হয়। নিনিয়ান ১৯৯৪ সালের অক্টোবর ঢাকায় আসেন। দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শেষে স্যার নিনিয়ান একটি সমাধান প্রস্তাব হাজির করেছিলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার থাকার কথা ছিল। আওয়ামী লীগ ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অচলাবস্থার অবসান হয়নি। অনেকের স্মরণে থাকবে, স্যার নিনিয়ানের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শাহ এ এম এস কিবরিয়া কমনওয়েলথ মহাসচিবের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে স্যার নিনিয়ান ‘পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন’।
এ রকম পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিভ মেরিল আলোচনার উদ্যোগ নেন। তাঁর সঙ্গে ছয়টি দেশের কূটনীতিকেরা যুক্ত ছিলেন বলে নিউইয়র্ক টাইমস–এর প্রতিবেদনে জানা যায়। ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতাসীন বিএনপির তত্ত্বাবধানে একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ওই সরকারকে স্বীকৃতি না দিতে ‘পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশকে’ আহ্বান জানিয়েছিলেন।
এ সময়ের স্বল্প আলোচিত কিন্তু সম্ভবত সফল প্রচেষ্টা হচ্ছে মার্কিন কংগ্রেস সদস্য বিল রিচার্ডসনের। মাত্র দুই দিনের সফরে এসে তিনি বলেছিলেন, সংকট সমাধানে তাঁর কাছে সুস্পষ্ট প্রস্তাব আছে। এ প্রস্তাবের বিস্তারিত প্রকাশিত না হলেও তিনি দুই নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ছয় দেশের রাষ্ট্রদূতেরা খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই খালেদা জিয়া বিরোধীদের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন ১৯৯৬ সালের ৩ মার্চ।
এ প্রস্তাবের ব্যাপারে এ ধরনের গুঞ্জন আছে যে মধ্যস্থতাকারীরা খালেদা জিয়াকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বিরোধীদের দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করে ক্ষমতার বাইরে থাকার সময় এবং নির্বাচনের পরে তাঁর বা তাঁর দলের ওপরে অন্যায় নির্যাতন চালানো হলে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হবে।
বিদেশিদের সংযুক্তির আরেক অধ্যায়ের সূচনা হয় ২০০১ সালের জুলাই মাসে। ছয় দিনের সফরে এসেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। তিনি দুই নেত্রীর সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন। কিন্তু তাতে দুই পক্ষের ভেতরে আস্থা তৈরি হয়নি। বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময়ে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ৫০ জন কূটনীতিকের কাছে ৫৫টি অভিযোগ করেছেন বলে ২০০৬ সালের ২১ মার্চ একটি সাপ্তাহিকে খবর বেরিয়েছিল।
২০০৬ সালের শেষ নাগাদ নেওয়া কূটনীতিকদের উদ্যোগ প্রায় সবার জানা ও বহুল আলোচিত। বাংলাদেশের আসন্ন রাজনৈতিক সংকট বিষয়ে উদ্বিগ্ন কূটনীতিকেরা আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে শুরু করেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পেট্রিসিয়া বিউটিনেস, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এবং ইউএনডিপির আবাসিক পরিচালক রেনেটা লক ডেসালিয়ন।
লক্ষণীয় অক্টোবর ২০০৬ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত কূটনীতিকদের এসব উদ্যোগকে কেউই ‘অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ’ বলে বর্ণনা করেননি। বরং দুই নেত্রী এবং তাঁদের দলের নেতারা এসব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের প্রস্তাব। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে হাসিনা একটি চিঠিতে এ অনুরোধ করেছিলেন।
উইকিলিকসের সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারির এক তারবার্তায় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ওয়াশিংটনকে জানিয়েছিল যে শেখ হাসিনা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ অধীনে নির্বাচনে তিনি রাজি আছেন। দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে, ১১ জানুয়ারির দুপুরে কূটনীতিকেরা আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কানাডার হাইকমিশনের বাসায়; সেখানেই তাঁরা জানিয়েছিলেন যে তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে ছয়জন কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন। রাতেই সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এ অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপের কারণেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল।
সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে যে অধ্যায়ের সূচনা, তার অবসান ঘটে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। আপাতদৃষ্টে এ সময়ে বিদেশি শক্তিগুলোর ভূমিকা ছিল না বলে মনে হলেও ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির আত্মজীবনী কোয়ালিশন ইয়ার্স ১৯৯৬-২০১২ (প্রকাশকাল: ২০১৭) থেকে জানা যায়, তিনি তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তিনি বিপদাপন্ন হবেন না।
শুধু তা–ই নয়, প্রণব মুখার্জি আওয়ামী লীগ নেতাদের এই বলে তিরস্কার করেছিলেন যেন তাঁরা কেন দলের নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াচ্ছেন না। আত্মজীবনীতে দেওয়া এই ভাষ্যে রাজনীতি এবং নির্বাচনে বিদেশি কোনো দেশের যে ভূমিকা তুলে ধরে, এর আগে আর কখনো কোনো দেশ বা তাঁর নেতা এই ভূমিকা রাখেননি। আক্ষরিক অর্থে এটি অভূতপূর্ব।
কিন্তু ২০১৭ সালে ইতিহাসের এই অধ্যায় জানার আগেই বাংলাদেশের মানুষ ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অভিজ্ঞতা লাভ করে। ২০১৩ সালের শেষ পর্যায়ে বিএনপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নির্বাচন বর্জনের পথে অগ্রসর হচ্ছে, সে সময় ঢাকা সফর করেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং। দুই দিনের সফরের সময় সুজাতা সিং জেনারেল এরশাদকে নির্বাচন বর্জনের পথ থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২২ ঘণ্টা অজ্ঞাতবাসে থাকার পর সুজাতা সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেই জেনারেল এরশাদ ঘোষণা দিয়েছিলেন, জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে।
এ সময় ভারতের অবস্থানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের ফারাক ছিল। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা ২০১৩ সালে একাধিকবার দিল্লিতে গিয়ে সবার অংশগ্রহণের মতো একটি নির্বাচনের জন্য ভারত যেন অবস্থান নেয়, সেটা বোঝাতে চেষ্টা করে সফল হননি (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আলী রীয়াজ, নিখোঁজ গণতন্ত্র, ঢাকা: প্রথমা, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৯৭-২০৫)।
ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেছিলেন, ‘দূতিয়ালি’ করার জন্য তিনি আসেননি, নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারত ‘সর্বোচ্চসংখ্যক’ দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন চায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভোটারদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। দূতিয়ালি করার চেষ্টা ছিল জাতিসংঘের। জাতিসংঘের মহাসচিবের দূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো বাংলাদেশে ২০১২ সালের ডিসেম্বর, ২০১৩ সালের মে এবং ২০১৩ ডিসেম্বরে ঢাকা সফর করেন। তঁার চেষ্টা সফল হয়নি। অথচ তখন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ, যার নেত্রী ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং পরে জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের কথা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছিলেন।
এক বছর ধরে যাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের কথা বলে আসছেন এবং এমন কথা বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ‘বিএনপির নিরাপত্তা সম্পাদক হয়েছেন’ (বিডিনিউজ ২৪, ৩ নভেম্বর ২০২৩), তাঁরা এ ধরনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ইতিহাসকে বিবেচনার বাইরের রাখেন।
যেটা আরও লক্ষণীয়, ১৯৯৬, ২০০৬ ও ২০১৩ সালের অভিজ্ঞতা বলে যে বাইরের শক্তিগুলোর সংশ্লিষ্টতা থেকে আওয়ামী লীগ বেশি লাভবান হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে এটাও দেখা যায়, বাইরের শক্তিগুলো নির্বাচন ও রাজনীতিকে তখনই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে, যখন দেশের রাজনীতিকে, বিশেষ করে রাজপথের রাজনীতিকে কোনো দল নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।
বর্তমান বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া দরকার
অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে যেসব ধারণা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ক্ষমতাসীনেরা এমন শিক্ষা নিতে পারেন যে নির্বাচনকেন্দ্রিক বিদেশিদের সংশ্লিষ্টতা, বিশেষ করে যারা অবাধ নির্বাচনের ওপরে জোর দিয়েছে, তাদের চাপ নির্বাচনের পরে কার্যত তেমন থাকে না। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বর্তমান বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নেওয়া দরকার।
বাংলাদেশের বর্তমান ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এটা মনে রাখা দরকার যে ২০২৩ সালে বিদেশি শক্তিগুলোর অবস্থান শুধু স্বার্থগত দ্বন্দ্বের বিষয় নয়, এর সঙ্গে আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রশ্নও জড়িত। ফলে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র-ভারত আলোচনার পর কোনো পক্ষের অবস্থান বদলে যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য শক্তিগুলো সরকারের আশ্বাস এবং ভারতের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে তাঁদের পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে, এমন ভাবলে ভুল হিসাব করা হবে।
বাংলাদেশের জন্য আগামী নির্বাচনের গুরুত্ব কেবল কে ক্ষমতায় থাকবে তা–ই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত আছে অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক রাজনীতির প্রশ্ন। অভ্যন্তরীণভাবে একটি কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকা না–থাকার প্রশ্নটি নির্ধারণের বিষয় হয়ে উঠেছে এই নির্বাচনে। অন্যদিকে ভবিষ্যতে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কী হবে, তার পথরেখার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।
এগুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশের নাগরিকেরাই কেবল উদ্বিগ্ন, তা নয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোও চিন্তিত। ফলে একটি অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে এবং এর মধ্য দিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে বিদেশিদের সংশ্লিষ্টতা ও চাপ দুটিই বাড়তে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের কথা বিবেচনা করলে এ ধরনের পরিস্থিতি সাধারণ নাগরিকদের জন্য একধরনের অশনিসংকেত।